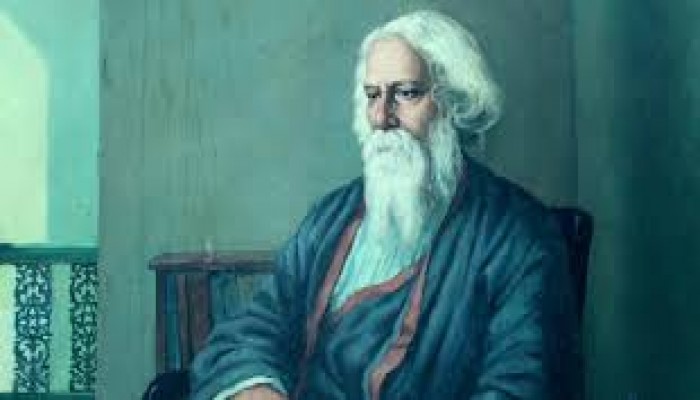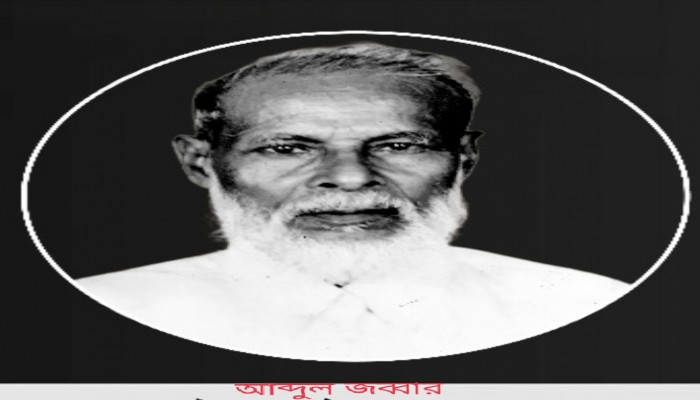কুমার সৌরভ::
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের স্মরণ অনুষ্ঠান একসাথে আয়োজন করার মাঝে অন্য ধরনের এক বিশেষত্ব রয়েছে। বাংলা ভাষার এই দুই মহৎ সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিকর্মে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁরা শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবজাত কোমল-কঠোর ভাবগাম্ভীর্যে আর নজরুল সহজাত বিদ্রোহী সত্তার তীব্রতা দিয়ে। আমরা সবসময় ভালো স্বদেশ, ভালো মানুষ, সকল মানুষের বসবাসের যোগ্য বসুন্ধরা দেখার বাসনা মনের ভিতরে পোষণ করি। এই ভালো কী ? ভালো মানে হলো সকলের জন্য ভালো। আমার জন্য ভালো আর দশজনের জন্য মন্দ; এমন অবস্থা কখনও সর্বজনীন ভালোর লক্ষণ হতে পারে না। এখন আমরা পৃথিবীকে গ্লোবাল ভিলেজ বলি। অর্থাৎ যোগাযোগ, প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে দুনিয়ার কোনো জায়গায়ই আমাদের কাছ থেকে অদৃশ্যমান অবস্থায় থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা যেমন বাঙালি বা বাংলাদেশী তেমনি বিশ^জনীন নাগরিকও বটে। কমিউনিজম এমন রাষ্ট্রবিহীন বৈষম্যমুক্ত বিশ্বের স্বপ্ন দেখিয়েছে। সেই স্বপ্ন অধরা থাকলেও মানব-ভাবনার বাইরে থাকে নি কখনও। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার পর দাস সমাজ ও সামন্ত সমাজ পেরিয়ে আমরা এখন পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীন। সমাজ পরিবর্তনে এর পরের ধাপ, মার্কসবাদীদের মতে-সাম্যবাদ, এর আগের স্থর সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র হয়ে সাম্যবাদে পৌঁছাতে পারলে মানবীয় বৈষম্য ও শোষণের অবসান ঘটবে। দুনিয়ার কিছু দেশে (রাশিয়া, গণচীন, কিউবা, ভিয়েতনামসহ বহু দেশ) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেও পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র ও সংশোধনবাদী তৎপরতায় তা ভেঙে পড়েছে। যেসব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো সেসব দেশে মানুষে-মানুষে শোষণের অবসান ঘটেছিলো, সর্বহারা একনায়কতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্রের সকল মানুষ সমানাধিকার ভোগ করতো। ‘রাশিয়ার চিঠি’ গদ্যগ্রন্থে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নজরুল সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নির্যাষ গ্রহণ করলে একটি সাম্যবাদী সমাজ চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। উভয়েই মানুষের উপর মানুষের শোষণ বন্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসন যেমন আমাদের বুকের ভিতর তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্রোহ তৈরি করে একইরকমভাবে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনও আমাদের ব্যথাতুর করে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ উন্মাদনায় আমরা আহত হই। আমরা যেমন বাংলাদেশের অর্থ পাচার করে বিদেশে কিছু মানুষের সম্পদের সুউচ্চ পাহাড় গড়ার দৃশ্য দেখে বৈষম্যবোধে তাড়িত হই তেমনি আন্তর্জাতিক পরিসরে সা¤্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের দ্বারা কম উন্নত দেশগুলোকে বাজার-কলোনি বানানোর আগ্রাসী তৎপরতায় আতঙ্কিত হই। আমরা ভাবি এই দেশ এই পৃথিবী দেখাই কি আমাদের জন্য অবধারিত ছিলো ? নাকি এর চাইতে ভালো দেশ ও বিশ^ দেখার সুযোগ ছিলো ? আমাদের এমন ভাবনার উত্তর মিলে রবীন্দ্র-নজরুলের সাহিত্যসম্ভারে। বিপর্যস্ত মানবতা, পদদলিত গণঅধিকার, শোষণ-শাসনের তীব্রতা, অস্ত্রের ঝনঝনানি, তৃতীয় বিশ^যুদ্ধের আশঙ্কা; সবকিছু মিলিয়ে বিশ^বাসী আজ এক সংকটজনক সময় অতিক্রম করছে। এমন সময়ে গণমানুষের ইতিকর্তব্য নির্ধারণে আমাদের বারবার রবীন্দ্র-নজরুলের কাছে ফিরে যেতে হবে। এই দুই মনীষীর যৌথ স্মরণ অনুষ্ঠানের সার্থকতা এই জায়গায়ই। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ১৮৬১ সনে। কাজী নজরুলের জন্মসন ১৮৯৯। রবিঠাকুরের জন্মের ৩৮ বছর পর নজরুলের জন্ম। রবিঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪১ সনে আর কাজী নজরুল ১৯৭৬ সনে। এখানেও সময়ের ব্যবধান ৩৫ বছর। মোটামুটি প্রায় সমান জীবনকাল পেয়েছিলেন এই দুই কবি। রবিঠাকুরের জীবৎকাল ৮০ বছর, নজরুলের ৭৭ বছর। আশ্চর্য কাকতাল হলো দুই কবিই জন্মেছিলেন মে মাসে, মৃত্যুবরণ করেন আগস্ট মাসে। এই দুই কাকতালের বাইরে রবিঠাকুর ও নজরুলের ভাবমানসে মিল-অমিল দুই-ই ছিলো প্রকটাকারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সাধনার জন্য পেয়েছিলেন মোটামুটি ৬৭ বছর। অকালে বাকরুদ্ধ হওয়ায় কাজী নজরুলের সাহিত্য সাধনার মেয়াদ ছিলো মাত্র ২০/২২ বছর। নজরুল যদি রবীন্দ্রনাথের সমান সময় সাহিত্য সাধনার সুযোগ পেতেন তাহলে বাংলা সাহিত্য নানা বৈচিত্রে আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতে পারত। রবিঠাকুর কবিতায় যেখানে নিমীলিত ভাবগাম্ভীর্যে ঋষিপুরুষ সেখানে নজরুল খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো তীক্ষ-তীব্র। উভয়ের সামাজিক অবস্থান এর পিছনে নির্ণায়ক ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করি। রবিঠাকুর জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় দারিদ্র্যতা ও সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার তীব্রতা নিজের জীবনে অনুভব করেন নি। কৃষক ও সাধারণ মানুষের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি জমিদারি পরিচালনাকালে। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই তাঁর গণমুখী কাব্যচর্চার উত্থান। এই পর্যবেক্ষণ সমাজের সাথে মিশে নয় বরং একটু দূরে অবস্থান করে সমাজ বাস্তবতা জানা ও বুঝার উপলব্ধি। অন্যদিকে নজরুল জন্মের পর থেকেই দারিদ্রতার সাথে লড়েছেন। জীবন ধারণের জন্য নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। তাই তাঁর পর্যবেক্ষণ একেবারে সমাজের ভিতরে অবস্থান করে নিজের জীবন থেকে অর্জন করা। এই দুই দেখার মধ্যে ব্যবধান অনিবার্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের শ্রেণি ও ভাবনাগত সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে নিপীড়িত মানুষের জন্য নজরুলকেই সামনে থেকে দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। কাজী নজরুলের ‘ধূমকেতু’ প্রকাশকালে দেয়া রবীন্দ্রনাথের আশীর্বচনে সেই আকাক্সক্ষা ফুটে উঠতে দেখি আমরা। কবিগুরু বলছেন, কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আঁধারে বাঁধো অগ্নিসেতু দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন অলক্ষণের তিলকরেখা রাতের ভালে হোক না লেখা জাগিয়ে দে রে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন। মানবতাবাদী রবিঠাকুর যখন বলেন- হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও স্থান অপমানে হতে হবে সবার সমান। (অপমানিত) অথবা নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। (প্রান্তিক কাব্যের ১৮ নং কবিতা) মানুষের অধিকারকাড়াদের অধিকারহারাদের মতো সমান অপদস্ত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছেন কবি। দানব তথা শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে শক্তি সহযোগে লড়াইয়ের আহ্বানও আছে। এই আকাক্সক্ষার মাঝে মানবতাবোধ, সংগ্রামশীলতা আছে কিন্তু আমরা যাকে শ্রেণি-চেতনা বলি তার অভাব লক্ষণীয়। কিন্তু কাজী নজরুল যখন বলেন- মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হব শান্ত। (বিদ্রোহী) অথবা ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল। আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই পায়ের সুখে ভাঙব চল ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল। তখন মনে হয় নজরুল এই সংগ্রামের নিজেই নায়ক। নিজেই বিদ্রোহের রক্তরাঙা লালপতাকা হাতে সব বৈষম্যের প্রাসাদ ভেঙে দিতে চান। এই জায়গায় নজরুলের নিজের জীবন সংগ্রাম থেকে আত্মস্ত করা শ্রেণি-চেতনা একেবারেই স্পষ্ট। রবীন্দ্র-নজরুলকে এক বৈঠকে পর্যালোচনা করা কখনও সম্ভব নয়। আমরা মরুভূমির এক দুই মুঠো বালুকণা নিয়ে কেবল দেখতে পারি তা সূর্যালোকের প্রখরতায় উত্তপ্ত নাকি নিষুতির আঁধার গায়ে মেখে উত্তাপ-হারানো। রবীন্দ্র-নজরুল বাগের যে বিশালতা সেখান থেকে যাবতীয় সুগন্ধে সুবাসিত হতে দরকার অনেক গভীরতা, সারা জীবনের অধ্যাবসায় এবং ভালোবাসা। আমরা এখানে কেবল এই দুই ফুল্ল কুসুমাস্তীর্ণ বিশাল উদ্যানের একটুখানি পাপড়ি স্পর্শ করে দেখার দুঃসাহস দেখাচ্ছি। সেই পাপড়ির নাম ‘মানুষ’- যে মানুষ চির অধিকারহারা, বঞ্চনায় বিদীর্ণ, শোষণ-শাসনে ত্রস্ত, অনাহারে ক্লিষ্ট, ভয়ে কাতর; সেই চেতনা কেড়ে নেয়া মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়ে দিতে নজরুল-রবি শব্দের উপর শব্দ গেঁথে যে চাবুক তৈরি করেছিলেন তাকে পরখ করে দেখার সামান্য চেষ্টা মাত্র। দুই বিঘা জমির উপেনের হাহাকার এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি- এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। ওই যে উপেনকে ভিটে ছাড়া করার ধনি শ্রেণির লুণ্ঠনবৃত্তি, রবিযুগ অতিক্রান্ত হলেও সামাজিক ওই ব্যাধি এখন আরও বেশি ভয়ানক চেহারা ধারণ করেছে। নিশ্চল চেতনার সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আজও সঠিক নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাবে দিশাহীন। ব্যক্তিগত মালিকানার দুর্ভেদ্য কারগার আমরা ভাঙতে পারি নি, একটু আঁচর লাগাতেও ব্যর্থ। এখনও সীমাহীন সম্পদ কুক্ষিগত করার মতলববাজি কায়েমে উপেনের মতো কোটি কোটি সাধারণ মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে অসহায়ভাবে ডুকরে কাঁদে। পৃথিবীর সম্পদভা-ারকে সামাজিক মালিকানাধীন মনে করার সাম্যবাদী চেতনা ‘এক পা এগোয় তো দুই পা পিছোয়’ দুরবস্থার মধ্যেই আমাদের ‘বর্তমান’ হতাশাজনক, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। মানুষ যদি নিজের অবস্থা পাল্টানোর জন্য নিজে সচেষ্ট না হয় তাহলে গায়েবি উপায়ে তার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ে যায় না। রবিঠাকুর তা বুঝেছিলেন। তাই ‘চালক’ কাব্যকণিকায় তিনি বলতে পেরেছেন- অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি। সেই আমি যতক্ষণ ‘আমরা সকলে’ যুথবদ্ধ হয়ে অদৃষ্ট বদলের লড়াইয়ে শামিল না হব ততক্ষণ এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। কবিও এমন মানুষের অগ্রবর্তী হওয়ার সন্ধান করেছেন। তিনি অন্য কারও পরিবর্তে নিজেকে রক্ষার জন্য নিজেরই শঙ্কাহীন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন- বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয়। দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত¡না, দুঃখে যেন করিতে পারি জয়। (আত্মত্রাণ) নজরুলও এমন মহামানবের উত্থান কামনা করেছেন কবিতার পঙক্তিতে। তিনি সদর্প উচ্চারণ করেছেন- পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে, মাথার উপর জ্বলেছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে। প্রার্থনা করো- যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস, যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ। (সর্বহারা) ওই ‘সোনার শত ছেলে’র উদ্দেশেই তিনি বলছেন- আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে- মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। জাগরণের এই বাণী দুই কবি বিলিয়েছেন মানবাত্মার মহামুক্তি তথা সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করতেই। তাঁরা আজ নেই। রবি-নজরুল চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে। কিন্তু তাঁদের দেখা পৃথিবীর সেই কুৎসিত চেহারার ইতিবাচক পরিবর্তন তো হয়ই নি বরং তা আরও কদাকার হয়েছে। সুতরাং আমাদের এখনও ‘হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনায় নজরুল’কেই ধারণ করতে হবে। শোষণহীন সাম্যের পৃথিবী দেখতে রবীন্দ্র-নজরুল থেকে শক্তি নিতে হবে। উপমহাদেশজুড়ে আজ মানুষে মানুষে বিভাজন। ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে, ভিন্নমতের কারণে, ভিন্ন সংস্কৃতির কারণে তৈরি হওয়া এই বিচ্ছিন্নতা আমাদের এমনভাবে গ্রাস করে রেখেছে যেখানে সর্বজনিন অগ্রগতি ও মিলন-বন্ধনের পরিবর্তে এইসব দেশে এখন নিষ্ঠুরতায় দমন-প্রবণতা ও একজনকে অপরজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয়েই বুঝেছিলেন এই ভূখ-ের শান্তি-স্থিতিশীলতার একটি বড় অন্তরায় এই বিভাজন। তাঁরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আত্মিক বন্ধন ও ঐক্য দৃঢ় করতে তাঁরা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিসত্তা, সৃষ্টিসত্তা সর্বক্ষেত্রেই ছিলেন মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক। ‘লোকহিত’ প্রবন্ধে তিনি বলছেন, ‘বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্ন-বস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করেছিলো। ... বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দেই নাই’। ‘সমস্যা’ প্রবন্ধেও তিনি অনুরূপ মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ধর্ম যখন বলে মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রি করো তখন কোনো তর্ক না করিয়াই কথাকে মাথায় করিয়া লইব। ...কিন্তু ধর্ম যখন বলে মুসলমানদের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করিবে না, তখন আমাকে প্রশ্ন করিতেই হইবে, কেন করিব না ?’ কাজী নজরুলও ধর্মের পরিচয়ের বাইরে মানুষ খোঁজেছেন আজীবন। তিনিও ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ-বিভাজনের বিরুদ্ধে কলমকে শাণিত রেখেছেন। ‘কা-ারী হুশিয়ার’ কবিতায় তিনি বলছেন, অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ, কা-ারী, আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ। ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম ?’ জিজ্ঞাসে কোন্ জন ? কা-ারী! বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার। সংকটকালে হিন্দু-মুসলমান পরিচয় না খোঁজে সকলকে মানুষ হিসেবে ভাবার জন্য দেশনেতৃত্ব তথা কা-ারীর প্রতি কবির এই উদাত্ত আহ্বান। ভারতবর্ষের সমন্বয়বাদী সমাজ-সভ্যতা ও পারস্পরিক সহাবস্থানের অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করে বিদ্রোহী কবি ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় লিখেছেন, গাহি সাম্যের গান- যেখানে আসিয়া এক হ’য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান, যেখানে মিশেছে হিন্দু-মুসলিম-ক্রীশ্চান। গাহি সাম্যের গান। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায়ই তার বজ্রনির্ঘোষ শোনতে পাই এই উচ্চারণে- ‘এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই’। ঠিক এমন মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ‘মানুষ’ কবিতায়, যেখানে কবি উচ্চারণ করছেন- ‘গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান’। মানুষের জয়গান গাওয়া এই কবি দুইজনই তো বিশ^জনীন মানবতার বিপন্নতার কালে বেশি বেশি চর্চিত হওয়া উচিৎ। আজ যখন মানবতা বিপন্ন, ধর্মীয় পরিচয়ের হিংসাশ্রয়ী বিভাজন রেখা ক্রমশ ক্রমবর্ধমান, তখন আমাদের রবীন্দ্র-নজরুলের কাছে বারেবারে মানুষ হওয়ার শপথ পাঠ করতে হবে। আমরা বিভিন্নভাবে রবীন্দ্র-নজরুলকে এখনও প্রাসঙ্গিক বলি। এর কারণ হলো সমাজ রূপান্তরের যে স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন, মানুষকে যে অনন্য উচ্চতায় তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁরা বিশ্বকে যেরূপ মানবীয় ও বৈষম্যমুক্ত হিসেবে চেয়েছিলেন; তার সবকিছুই অনর্জিত থাকা। এখনও তাঁদের কালজয়ী কথায় আমরা উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পাই। পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার চেতনার সন্ধান পাই। তাই তাঁদের ভুলা কখনও সম্ভব নয়। শতবর্ষ পরে রবিঠাকুর যে নতুন কবির অভ্য্যুদয় কামনা করেছেন তাঁর কবিতাখানি কৌতূহলভরে পড়ার জন্য, তা মূলত সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এই সময়কে বিশ্লেষণ করার আকাক্সক্ষাজাত। ‘কতকথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়, কত অনুরাগে’ সেই অনুরাগ জাগানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাত্যহিক চর্চার বিষয়বস্তু। একইসাথে কাজী নজরুলও সেই যে বলেছিলেন, ‘আমি চিরতরে চলে যাব, তোমাদের দিব না ভুলিতে’, আমরা কি তাঁকে ভুলতে পারছি ? পারছি না বলেই আমরা আজ এখানে তাঁদের অমর জীবনের কিছু অধ্যায় খোঁজতে সমবেত হয়েছি। কালোত্তীর্ণ এই মহান কবি দুইজনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করি। একইসাথে তাঁদের চেতনায় হৃদ্ধ হওয়ার শপথ নেই। ধন্যবাদ সকলকে।
(রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠানে পঠিত)
নিউজটি আপডেট করেছেন : SunamKantha
রবীন্দ্র-নজরুল চিন্তায় মানবমুক্তি
- আপলোড সময় : ২৮-০৫-২০২৫ ০৮:৫৫:৫৪ পূর্বাহ্ন
- আপডেট সময় : ২৮-০৫-২০২৫ ০৮:৫৬:৩৫ পূর্বাহ্ন

কমেন্ট বক্স
সর্বশেষ সংবাদ
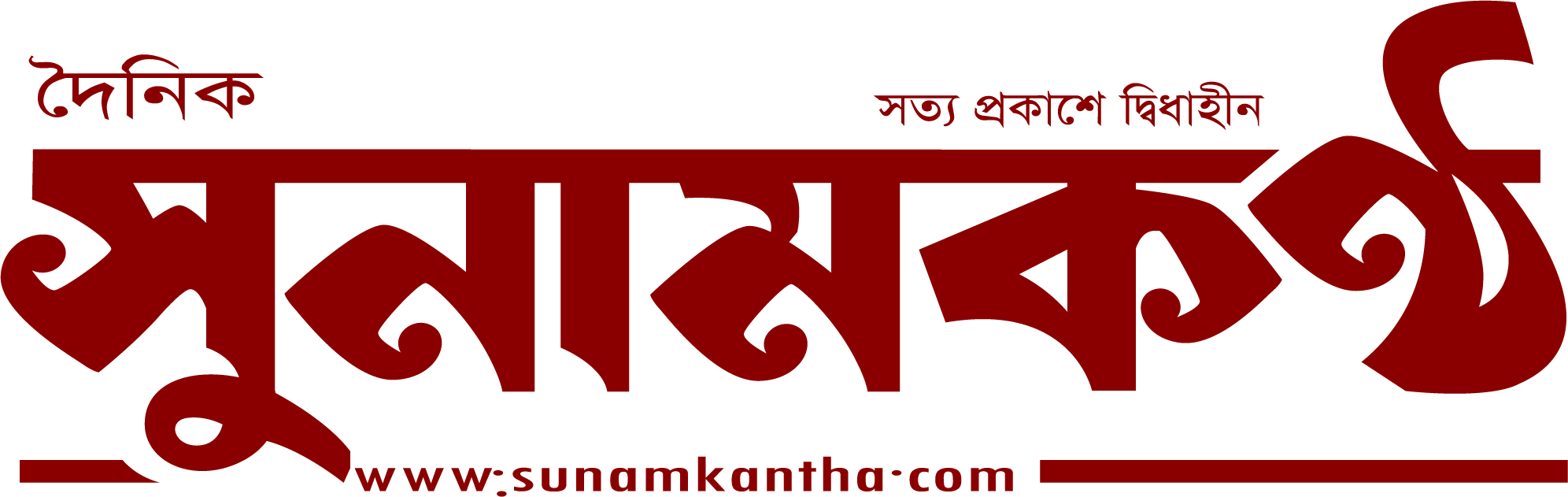
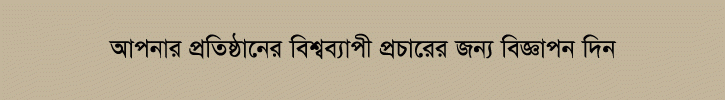

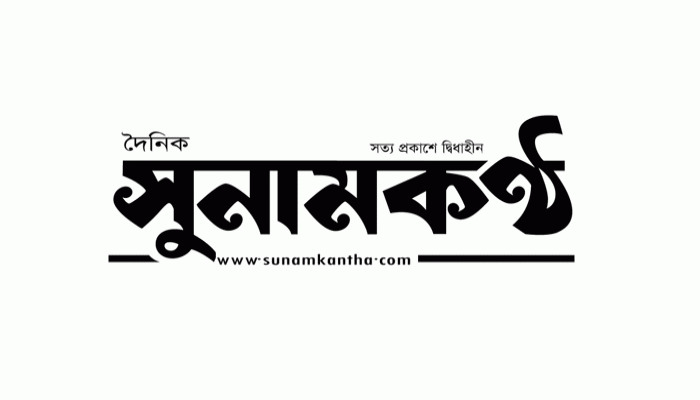 সুনামকন্ঠ ডেস্ক
সুনামকন্ঠ ডেস্ক